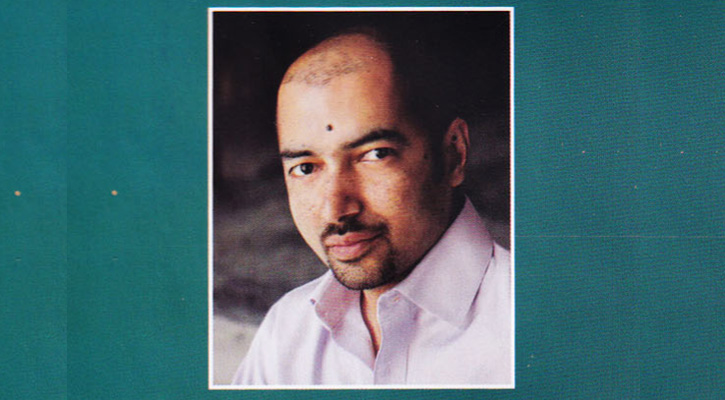
কাজী আনিস আহমেদ, ফাইল ফটো
১. রূপকথা
‘ঠাকুরমার ঝুলিটির মত এত বড় স্বদেশী জিনিস আমাদের দেশে আর কি আছে? কিন্তু হায় এই মোহন ঝুলিটিও ইদানীং ম্যাঞ্চেস্টারের কল হইতে তৈরী হইয়া আসিতেছিল। এখানকার কালে বিলাতে 'Fairy Tales' আমাদের ছেলেদের একমাত্র গতি হইয়া উঠিবার উপক্রম করিয়াছে। স্বদেশের দিদিমা কোম্পানী একেবারে ‘দেউলে’। তাঁদের ঝুলি ঝাড়া দিলে কোন কোন স্থলে মার্টিনের এথিক্স এবং বার্কের ফরাসী বিপ্লবের নোটবই বাহির হইয়া পড়িতে পারে, কিন্তু কোথায় গেল রাজপুত্র পাওরের পুত্র, বেঙ্গমা-বেঙ্গমী, কোথায়- সাত সমুদ্র তেরো নদী পারের সাত রাজার ধন মাণিক।’
দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার সংগৃহীত ‘ঠাকুরমার ঝুলি’র ভূমিকা লিখলেন রবীন্দ্রনাথ ১৩১৪ সনের ২০ ভাদ্র, বোলপুর বসে। ‘ঠাকুরমার ঝুলি’ প্রকাশিত হয় ১৩১৪ বঙ্গাব্দে। ১১২-১৩ বছর পরও তার মহিমা বিদ্যমান।
এ কথা মনে এল কাজী আনিস আহমেদের ‘চল্লিশ কদম’ নামের আখ্যানটি পড়তে পড়তে, যা ২০০৬ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় একুশে বইমেলায় বাংলাদেশে।
আনিস বইটি নির্মাণ করেছেন ইংরেজি অক্ষরে। তার সুচারু বঙ্গানুবাদ করেছেন সদ্য প্রয়াত অধ্যাপক, অনুবাদক, কবি ও আখ্যানকার মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দীর্ঘদিন-বহু বছর আলাপের সূত্রে জানি কী চমৎকার ডিটেকটিভ গল্প লিখতেন তিনি। শর্শবর দত্ত প্রণীত ‘দস্যু মোহন’-এর সব কটি খণ্ড দেখেছি মানবদার হরিপদ দত্ত লেনের বাড়িতে। টালিগঞ্জে ‘নবীনা’ সিনেমার থেকে অল্প দূরে, হয়তো একটু পেছন দিকেও, ভাড়া বাড়িতে-একতলায় থাকতেন মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
এ কথা বলার অর্থ এই নয় যে, দস্যুমোহন, তার ভালোবাসার নারী-রমা ইত্যাদি প্রভৃতির সঙ্গে মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিটেকটিভ গল্প মেলে। মানবদার গোয়েন্দা কাহিনি যে সম্পূর্ণ ভিন্নতর, তা বলার কোনো অবকাশই রাখে না। তাঁর নির্মিত খেলার প্রতিবেদন পড়েছি পাক্ষিক ‘প্রতিক্ষণ’-এর পাতায়। ‘প্রতিক্ষণ’-এর প্রথম দিকে তো প্রায় নিয়মিত লিখতেন। খেলা ও রাজনীতি, যার মূল সুরটুকু এমনই তো ছিল।
মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ই আমাদের সামনে, বাংলা ভাষায় প্রথম তুলে ধরেন কমিকসের রাজনৈতিক ভাষ্য। অরণ্যদেব বা বেতাল, ডায়না পামার, মজ বুড়ো, গুরান-পিগমি সর্দার গুরান, কিলাউয়ির সোনা বেলা, খুলি গুহা, কুকুর নাকি নেকড়ে ‘বাঘা’, অরণ্যদেবের ঘোড়া ‘তুফান’ অথবা ‘হিরো’ রেক্স-রাজা-সবই যে আসলে সাম্রাজ্যবাদীদের প্রচার ফ্রেমে আঁটপাট বাঁধা, বর্ণবিদ্বেষী সূত্র ধরেই চলে আসে আমাদের সামনে, এমনটাই যথেষ্ট যুক্তি দিয়ে বলেন অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়।
শুধু বলেন না, লেখেনও।
এভাবেই রিপ কার্বি নামের বুদ্ধিমান গোয়েন্দাটি, তার বাটলার কাম সহকারী ডেসমন্ড, জাদুকর ম্যানড্রেক, ম্যানড্রেক সঙ্গী লোমার, জানাডু নামের অতি সুরক্ষিত শহর, ম্যানড্রেক মুগ্ধ সুন্দরি নার্দা জাদুকর ম্যানড্রেকের বাবা-অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন মেরন, সবটাই যে আসলে সাম্রাজ্যবাদীদের চাপিয়ে দেয়া কু-প্রহর বার্তা, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তা আমাদের বুঝিয়ে দেন প্রায় হাতেধরে। এমনকি মেরনের কাছে থাকা বিশেষ শক্তি-অবশ্যই তা অলৌকিক, সেই স্ফটিকখ-টিকেও চুলচেরা বিশ্লেষণে সাজান মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
এভাবেই সামনে আসে ফ্ল্যাশ গর্ডন। মহাকাশ অভিযাত্রী এই অতি ক্ষমতাসম্পন্ন জনের বিষয়টিও তিনি বুঝিয়ে দেন আমাদের। সেইসঙ্গে টিনটিন। তখন ‘টাইমস অব ইন্ডিয়া’র ইন্দ্রজাল কমিকসে ফ্ল্যাশ গর্ডন, বেতাল।
হার্জ বা আরজ নির্মিত কমিকস টিনটিন, সঙ্গে টিনটিনের পোষা কুকুর স্রোয়ি-বাংলা করার সময় তার নাম হয়েছে কুট্টুস। সেইসঙ্গে মদ ভালোবাসা, দেড়েল ক্যাপটেন হ্যাডক, দুই গোয়েন্দা হবমন অ্যান্ড জবসন (কে জানে এই ডিটেকটিভ যুগলের নাম ঠিক লিখলাম কি না, জনসন হবে কি, জবসনের বদলে? তো যাকগে যাক, নামে কী এসে যায়, না, না যায়ও, সব বাহাস বন্ধ করে কথায় ফিরি, পুনর্বার।)।
বেলজিয়ান চিত্রকর হার্জ বা আর্জ, যে চরিত্রদের সৃষ্টি করলেন টিনটিন কমিকসের মধ্য দিয়ে, এইরে এবার বোধ হয় মনে পড়ল সেই জোড়া ডিটেকটিভের নাম-খম্পসন অ্যান্ড থম্পসন সেই অতি ফানি, টেকো, মাথায় কালো টুপি পরা, হাতে লাঠি গোয়েন্দাদের নাম। এই বাক্য লিখেই মনে হচ্ছে, এই রে, গোয়েন্দা নামে কোথাও ভুল হলো না তো? তো থাক সে সব প্রসঙ্গ। আপাতত মানবেন্দ্রদাতে ফেরা যাক।
টিনটিন ক্যাপটেন হ্যাডক, যার অতি বিখ্যাত সব গালি সমন্বিত ডায়ালগের মধ্যে একটি-‘ব্লিস্টারিং ব্রিংকিলস’, ‘থান্ডারিং’, ‘টাইফুন’ ইত্যাদি তো সে যাকগে, এই বেলজিয়ান স্রষ্টার আপাত-নিরীহ, অতি কচি টিনটিনও যে প্রকৃত প্রস্তাবে সাদা চামড়া, কালো চামড়া বিভাজনতত্ত্বে বিশ্বাসী একজন স্কিন হেটার-ধর্মবিদ্বেষী, এটাও তিনি আমাদের বুঝিয়ে দিতে পারেন অতি সরলভাবে।
আখ্যানকার কাজী আনিস আহমেদের বঙ্গানুবাদে ‘চল্লিশ কদম’ নামে বইটি যখন অনুবাদকর্মের জন্য মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিচ্ছে কবি ও ভাবুক, সাংবাদিক, হৃদয়বান বন্ধু শামীম রেজা, তখন নানাভাবে, বিভিন্ন সময়ে উপস্থিত থেকেছি তাঁর সঙ্গে মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সকাশে। সে-ও এক চমৎকার অভিজ্ঞতা।
তত দিনে অবশ্য হরিপদ দত্ত লেনের ভাড়াটে আবাস ছেড়ে মানবদা চলে গেছেন বনডেল গেট ছাড়িয়ে একটি ফ্ল্যাটে। বেশ বড়সড়, প্রশস্ত সেই ফ্ল্যাটবাড়িতে তিনি, সঙ্গে তাঁর অজস্র বই, ম্যাগাজিন-বলা যেতে পারে দেশি-বিদেশি গ্রন্থসাগর। আর একজন সর্বক্ষণের কর্মসহায়িকা। সম্ভবত মালতীই তাঁর নাম। তিনিই মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংসার সামলান।
সেই নতুন আবাসনে যাওয়া-আসায় খুবই তকলিফ। এমনকি ট্যাক্সিও যেতে চায় না সব সময়। ফেরার পথে ট্যাক্সি পাওয়া আর লটারির টিকিট কেটে টাকা জেতা-একই ব্যাপার প্রায়।
এইটুকু তথ্য এই জন্যই দেয়া আখ্যানকার কাজী আনিস আহমেদের কৃশ, অথচ ভাবনাবৃত্ত ও চিন্তা-চৈতন্য তার বহু বিস্তৃত, সেই গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদের কিছু স্মৃতি এখনো জেগে আছে, তা আরও বেশি বেশি উলসে-উসকে উঠল ‘চল্লিশ কদম’ নিয়ে কিছু লিখতে গিয়ে। এই আখ্যান পুনরায় পাঠ করতে করতে সদ্য প্রয়াত অধ্যাপক মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কালযাপনের নানা স্মৃতিও মনে এল, তাই এই গোড়াপত্তনীয় উপস্থাপনা।
২. গল্পের এক যে ছিল
আমাদের এই উপমহাদেশে আখ্যানকলা নির্মিতির একটি ছকভাঙা চলন আছে। সেই আদরা বা মডেল আসলে কোনো আদরা বা মডেলই নয়, যে অর্থে ইউরোপ, বিশেষ করে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের ছক বাঁধা বক্তব্য আমাদের আখ্যান তুষ্টির একটি ক্রম সংকেত তৈরি করে ও তারে বেঁধে দেয়। আর এই ঔপনিবেশিক বন্ধনকে বারেবারে অস্বীকার করেন একজন কথাকার ও কবি। চলচ্চিত্র নির্মাতা, নাটককার, ছবি আঁকিয়ে, গাইয়ে মূর্তি নির্মাতা।
ফলে যামিনী রায় উপনিবেশকালের মধ্যেই ঔপনিবেশিক ছবিযন্ত্রকে অস্বীকার করেন, ভাঙতে থাকেন। একইভাবে জয়নুল আবেদিন, পরবর্তী সময়ে কামরুল হাসান, গণেশ পাইনরা উপনিবেশের শৃঙ্খল ঝঞ্ঝাকে মেনে তো নেনই না, বরং স্বদেশ-চৈতন্যের প্রতীক নির্মাণে হয়ে ওঠেন কলোনি, কলোনি ভাবনা, কলোনিয়াল লিগ্যাসির প্রতিস্পর্ধা।
গণেশ পাইন তাঁর সামগ্রিকতায় এক ঐতিহ্য দিয়ে নির্মাণ করেন নব ঐতিহ্য। প্রতিভাবান চিত্রকর কামরুল হাসানও তাই।
যামিনী রায় তাঁর অঙ্কনযাত্রার প্রথম দিবসে-প্রদোষকালে ইউরোপীয় অঙ্কনকলা ইম্প্রেশনিজমের দ্বারা প্রভাবান্বিত ছিলেন ভীষণভাবে। এই সত্য উপলব্ধি করা যায় যামিনী বাবুর একেবারে গোড়ার দিকের চিত্র নির্মাণে নজর করলে।
যামিনী রায় ‘যামিনী পটুয়া’ হলেন ভারতীয়, তথা বাংলার পট আঙ্গিককে নিজের ছবিতে নিয়ে এসে। তাঁর উত্তরকালীন চিত্রমোহাঞ্জনে তাই প্রভু যিশু, জোসেফ, মাতা মরিয়ম, এমনকি গাধাটিও বাংলার লোকচিত্রের অনুগামী হয়ে ওঠে সচেতনভাবেই।
বিশিষ্ট কবি বিষ্ণুদের সান্নিধ্য যামিনী রায়কে আরও অনেক অনেক বেশি তীক্ষ্ণ, সচেতন, সতেজ করে তোলে।
আমাদের মনে আছে, অখ- বঙ্গের বাঁকুড়ার বেলেতোড় বা বেলিয়াতোড়ের গ্রাম থেকে যামিনীবাবু শহর কলকাতার বাগবাজারে চলে এলেন। স্টুডিও তৈরি করলেন নিজস্ব ঢঙে। প্রখ্যাত কথাকার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন যামিনীবাবুর প্রতিবেশী। একসঙ্গে বাজারে যেতেন তাঁরা। সেটা তিরিশের দশকের প্রায় শেষ সময়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আসব আসব করছে। অ্যাডলফ হিটলার, বেনিতো মুসোলিনি, জোসেফ স্তালিন, জাপান সম্রাট তোজো, রুজভেল্ট, উইনস্টন চার্চিল-এই সব নামে নামে মথিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক রাজনীতির বাতাস।
আমাদের অখ- দেশ বারেবারে শুনতে পাচ্ছে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, মহাত্মা গান্ধী, মওলানা আবুল কালাম আজাদ, সরদার বল্লভভাই প্যাটেল, খান আবদুল গফফর খান প্রমুখ জাতীয়তাবাদী জাতীয় নেতার নাম।
ইতিহাস তৈরি করছেন চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহের সর্বাধিনায়ক ‘মাস্টারদা’ সূর্য সেনের নেতৃত্বে নির্মল সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী, লোকনাথ বল, প্রীতিলতা ওয়াদেদ্দার, গণেশ ঘোষ, কল্পনা দত্ত (যোশী), তারকেশ্বর দস্তিদার, হরিগোপাল বল (টেগরা), অনন্ত সিংহ, মাখন (জীবন ঘোষাল) প্রমুখের আত্মবলিদান, ফাঁসির মঞ্চ, দ্বীপান্তর, গুলিযুদ্ধ অথবা পটাসিয়াম সায়ানাইডের ‘হে মোর মরণ, হে মোর মরণ’ উচ্চারণে।
আসফাকউল্লা, চন্দ্রশেখর আজাদ, ভগৎ সিং, রাজগুরু, শুকদেব, উধম সিং, মদনলাল ধিংড়া, কত কত প্রাণ যে বলি হলো স্বাধীনতাযুদ্ধে!
বিনয় বসু, বাদল (সুধীর) গুপ্ত, দীনেশ গুপ্ত, প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য, বীণা-শান্তি-সুনীতি, ভবানী ভট্টাচার্য। কত কত শহীদের নাম ভেসে ভেসে আসে সামনে।
ক্ষুদিরাম বসু, প্রফুল্ল চাকী তিন ভাই চাপেকার-বিনায়ক, বিনয়হরি, দামোদর, সমস্ত শহীদ এসে দাঁড়িয়ে যান জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের কথা লেখার সময়।
আমরা খুঁজে পাই তুখোড় মস্তিষ্কসম্পন্ন, ছদ্মবেশ ধারণে অতি দক্ষ রাসবিহারী বসুকে। যিনি রবীন্দ্রনাথের আপ্তসহায়ক, এই পরিচয়ে পিএন টেগোর ছদ্মনামে চলে গেলেন জাপান। তার আগে পরিকল্পনা করেছিলেন দ্বিতীয় সিপাহি বিদ্রোহের। সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় বিশ্বাসঘাতকতার কারণে।
যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন), নিরালম্ব স্বামী, নানা সাহেব, তাঁতিয়া তোপে, ঝাঁসির রানি লক্ষ্মী বাই, কুনওয়ার সিং, সুভাষ চন্দ্রের-নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর আইএনএ-আজাদ হিন্দ ফৌজ, তার বীর সেনানীরা, শাহনওয়াজ, সেহগল, ধিলোঁ, লক্ষ্মী সেহগল- ‘কদম কদম বঢ়ায়ে যা...’।
অনেকেই, হয়তো অনেকে নয়, কেউ কেউ ভাবতেই পারেন আখ্যান নির্মাণ ভারতীয় আখ্যানকলার শিকড়সন্ধানে এত এত স্বাধীনতাযোদ্ধার নাম কেন উঠে আসছে?
এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, ঔপনিবেশিক জন্ডিতের ছেঁড়ার যাত্রাপথে এসব অগ্নিকন্যা, অগ্নিপুত্রদের পাশাপাশি, উপনিবেশের চাপানো আখ্যানগণ্ডি-লক্ষ্মণরেখা ভাঙাও হয়ে ওঠে উপনিবেশকে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যানের আদরা। কলোনিয়াল মডেল ভেঙে নতুন এক আপন যাত্রাপথে অগ্রসর হওয়া।
তাই ধর্মমঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল আমার ছাতিসত্তার আদি আখ্যানচিহ্ন। যদি বিক্রম শেঠের ‘গোল্ডেন গেট’কে উপন্যাস বলা হয়, সেই যুক্তিতে ধর্মমঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল আখ্যান তো হয়ে উঠবেই।
ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘নববাবু বিলাস’, ‘নববিবি বিলাস’, ‘কলকেতার নুকোচুরি’ আমাদের বাংলা ও বাঙালির আদি আখ্যানের চিহ্নবিন্দু। কালীপ্রসন্ন সিংহ, যিনি বাংলা মহাভারতের অন্যতম রূপকার, পাশাপাশি ‘হুতোম পেঁচার নকশা’ নামে এক আশ্চর্য গ্রন্থ প্রণেতা, সেই হুতোমি গদ্যকে যদিও বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় খুব একটা পছন্দ করেননি, কিন্তু হুতোমি গদ্য ও ‘হুতোম পেঁচার নকশা’ বাংলা ও বাঙালির আদি আখ্যানযাত্রার রূপকল্প।
প্যারীচাঁদ মিত্রের ‘আলালের ঘরের দুলাল’ আলালি গদ্যের এক নতুন দিকদর্শন উপস্থিত করে আমাদের সামনে। প্যারীচাঁদ মিত্র টেকচাঁদ ঠাকুর-এই ছদ্মনামে লিখতেন।
বাবু বঙ্কিমচন্দ্র এই আলালি গদ্যকেও নেকনজরে দেখেননি। কিন্তু ‘আলালের ঘরের দুলার’-এর গদ্যরীতি আমাদের চৈতন্যগভীরে উপনিবেশ অস্বীকারের প্রাণমন্ত্র বুনে দিয়ে যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের ‘কমলাকান্তের দপ্তর’ ও ‘মুচিরাম গুড়’ একইভাবে ঔপনিবেশিক শৃঙ্খল অস্বীকার করে হয়ে ওঠে বাংলা আখ্যানের আদি বীজতলা।
প্রাচ্যের লিখন আদরায়-আমি আমাদের আপাত-খণ্ডিত এই ‘বত্রিশ পুতুলের উপাখ্যান’, ‘কথা সরিৎ সাগর’, ‘জাতক কাহিনি’ বিভিন্ন আখ্যান বন্দিশ আমাদের সামনে উপনিবেশের চাপানো সংজ্ঞা শিল্প বিপ্লব ও উপনিবেশ সন্ধানে যাত্রা, টানা সমুদ্র অভিযান ইত্যাদি জন্ম দিয়েছে ছোট গল্পের, তাকে অস্বীকার করে।
ঔপনিবেশিক ইউরোপ, গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, পর্তুগাল, স্পেন, ইতালি, বেলজিয়াম, ওলন্দাজ ও দিনেমাররা যাকে দেশ আবিষ্কার, দুঃসাহসিক সমুদ্র অভিযান-‘ভয়েজ’, ‘এক্সপিডিসান’ ইত্যাদি বলছে, আসলে তা তো দেশ দখল, বাজার দখলের-বাজার সম্প্রসারণের পরিকল্পনা, নিখুঁত ছক ধরে যা এগোতে থাকে। আর তারই ফলাফলে এশিয়া, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা (সাম্রাজ্যবাদীদের দেয়া নাম ‘লাতিন আমেরিকা’) দখলদার ঔপনিবেশিকদের কাঁটা মারা বুটের তলায়, শৃঙ্খলের ঝনৎকার, কণ্টকগ্রাসে থাকা চাবুকের হিস হিস, বন্দুক-কামানের নির্ঘোষ গুলি-গোলা ফাটানোর অতি তীব্র শব্দ, বারুদ আর রক্তের ঝাঁজালো, কটুবাস সব মিলিয়ে ও উপনিবেশ, হে উপনিবেশ, হে দুর্ভাগা ‘কলোনিয়াল ম্যান’।
প্রাচ্যের আরেকটি জ্ঞানধারা আরব্য রজনীর গল্প-‘আরব্য উপন্যাস’, ‘পারস্য উপন্যাস’। ‘আলিফ লায়লা’র মোহময় ‘প্রাণকেলি’তে থেকে যায় চাপা যৌনতা ও যৌন আবেশের নিভৃত, কখনো কখনো প্রকাশ্য সঞ্চারও। ফলে ‘এলিট’, ‘লেখাপড়া জানা’, খানিকটা ব্রিটিশঘেঁষা-ঔপনিবেশিকদের দাক্ষিণ্যে বাঁচা হিন্দু বাঙালির একটি অংশকে ‘আরব্য রজনী’র গার্হস্থ্য সংস্করণ প্রকাশের কথা ভাবতে হয়। ব্রাহ্ম ভাবধারার প্রভাবও পড়ে তার ওপর। ফলে ভিক্টোরিয়ান ‘শুচিবায়ুগ্রস্ত’ ব্যাপারটি তথাকথিত ‘এলিট’ বাঙালির ভাবনা-চৈতন্যেও খানিকটা প্রভাব বিস্তার করে।
এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ‘নষ্টনীড়’-এর ভূপতি চরিত্রটির কথাও বলা যায় অনায়াসেই।
আপাতত তোলা থাক ‘নষ্টনীড়’ অথবা ‘চারুলতা’ প্রসঙ্গ। প্রাচ্যের রাত্রিব্যাপী নিশিজাগরণের ‘আলিফ লায়লা’, আরব্য রজনীকথার সৌন্দর্যময় বাদশাহজাদা শাহরিয়ার সবই একপর্যায়ে এসে সময় হারিয়ে সময়ান্তরে যাওয়ার মায়াদর্পণ হয়ে ওঠে অনায়াসেই। সেই মায়ামুকুর যেমন আলোকবিচ্ছুরণ, ছবিদারি করে, তেমনই টুকরো টুকরোও হয়ে যায় অবলীলায়।
ভাঙা দর্পণও উপনিবেশকে অস্বীকারই করে না শুধু, তার দিকে ছুড়ে দেয় মস্ত এক চ্যালেঞ্জও। সেই প্রতিস্পর্ধার নাম ঔপনিবেশিকতার সাহিত্যভাবনার বিপ্রতীপ স্রোত।
আমাদের এই আপাত-খণ্ডিত উপমহাদেশ-ভারতবর্ষ, বাংলাদেশ, পাকিস্তানে গল্পের কল্পবৃক্ষ মাথাচাড়া দিতে থাকে নানি, দাদি, ঠাকুমা, দিদিমা, মা-মামি, জেঠিমা, কাকিমা-খুড়িমা, আজিমা, আম্মা, খালা, চাচিমাদের স্মৃতিবন্দী কাহিনির উজান বহে যাওয়ার মধ্যে।
কথারা প্রকাশ্যে আসে রাজা, বাদশা, রানি, বেগম, সতিন কাঁটা, বাঁদি, দাসী, মুকুতা ফলের গাছ, কল্পতরু, পাখামেলা, ডানাদার ঘোড়া-পঙ্খীরাজ, মাথায় গজমুক্তা বহনকারী রাজহস্তী, ব্যাঙ্গমা আর ব্যাঙ্গমী নামের দুই রূপপক্ষী- যারা থাকে রূপকথারই জগতে, সেইসঙ্গে রাক্ষসী রানি, সুয়োরানি, দুয়োরানি, কইড়া জাঙাল, হাড়ের পাহাড়, কড়ির পাহাড়, লালকমল-নীলকমল, রানির হাড় মুড়মুড়ি ব্যারাম, বাঁদর রাজপুত্র, সোনার কাঠি-রুপোর কাঠি-সব-সবটুকু নিয়ে।
রূপকথার এই জগৎ বড় মনোহর। সেখানে সব সময়ই গল্পের এক যে ছিল ‘জো হুজুর’ না বলেই হুজুরে হাজির।
যেমন ধরা যাক ‘ঠাকুর মা’র ঝুলি’র প্রথম আখ্যানটি ‘কলাবতী রাজকন্যা’। এই আখ্যানের প্রথম লাইনটিই হলো-
‘এক যে, রাজা। রাজার সাত রাণী।-বড়রাণী, মেজরাণী, সেজরাণী, ন-রাণী, কনেরাণী, দুয়োরাণী আর ছোটরাণী।’
এই যে আখ্যানের শুরুয়াত, ‘এক যে ছিল’, এ তো প্রাচ্য আখ্যানরীতির অন্যতম ধরতাই।
চিৎপুরে ছাপা ইসলামি পুথি- ‘সোহরাব-রোস্তমের জং’, ‘চাম্পাবতী গাজি কালু’র উপাখ্যান বা আরও আরও যে সমাহার সৌষ্ঠব, তার চিত্রময়তাতেও তো বিলাপী সৌন্দর্য আর সেই আখ্যানের ‘এক যে ছিল ...’।
এই ‘এক যে ছিল’ ‘এক যে ছিল বাঘ’ হতে পারে। হতে পারে ‘এক যে ছিল দেশ’, হওয়া সম্ভব- ‘এক যে ছিল রাজা, তার ছিল দুই রানি, দুই রানি- সুয়োরানি আর দুয়োরানি। রাজার ছিল হাতি শালে হাতি, ঘোড়া শালে ঘোড়া...’ ইত্যাদি প্রভৃতি।
রূপকথায় সোনার কাঠির ছোঁয়ায় জেগে ওঠে পরম রূপময়ী রাজকন্যা কাঞ্চনমালা। রুপোর কাঠির স্পর্শে সে আবার পড়ে ঘুমিয়ে। কল্পনার মায়াতরু, ডানা ঝাপটানো সাদা পঙ্খীরাজ, পঙ্খীরাজ ঘোড়া, কথাবলা গাছ, কথক নদী-সবই প্রাচ্যের আখ্যানের ভরবিন্দু।
দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, রেভারেন্ড লালবিহারী দে সেই সব কথন-পুত্তলির সংগ্রাহক মাত্র। অতি গুরুত্বপূর্ণ তাঁদের সেই কুড়িয়ে নিয়ে গুছিয়ে রাখা।
চিৎপুরে ছাপা ইসলামি পুঁথিও উপনিবেশকালেরই। কিন্তু ছন্দ নির্যাসে তা-ও যেন হয়ে ওঠে ঔপনিবেশিক স্পর্ধার বিরুদ্ধে দাঁড়ানো তিতুমীরের দ্রোহী বাঁশের কেল্লা।
৩. এবার ‘চল্লিশ কদম’
‘আগের সন্ধ্যাতেই মারা যাওয়ার পর শিকদার সাহেব এখন মাটির ছয় ফিট তলায় শুয়ে আছেন। মারা যে গেছেন সে সম্বন্ধে নিজে তিনি খুব একটা নিশ্চিত ছিলেন না বটে, তবে যাঁরা তাঁকে কবর দিয়েছিল তাঁরা অবশ্য পুরোপুরি নিঃসন্দিগ্ধই ছিল। সাদা কাফনে আপাদমস্তক ঢাকা, সেখানে শুয়ে শুয়ে এখন তাঁর মুনকার আর নাকির এই দুই ফেরেশতার জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছুই করার নেই।’
‘তাঁর শুধু মনে পড়ছে যে তিনি মোল্লার খোঁজে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু ঠিক তারপরেই কখন কী ঘটে গেল সে সম্বন্ধে তাঁর স্মৃতি আদপেই পরিষ্কার নয়। আর, যদিও তাঁর মনেই পড়ে না কখন তাঁকে গোর দেয়া হয়েছিল, তবে কোন কোন ঘটনা তাঁকে এমন দুর্দশায় এনে ফেলেছে, তার একটি আনুপূর্বিক পরম্পরা ভেবে নেয়ার চেষ্টা করলেন তিনি, যখন তিনি ধানক্ষেতের মাঝে একটা আলের ওপর দাঁড়িয়ে ছিলেন, তখনই আচমকা সংজ্ঞাহারা হয়ে ভুঁয়ে লুটিয়ে পড়েছিলেন (তবে স্মৃতির সেই ছবিটা হয়তো তাঁর মনে গেঁথে আছে আগে যতবার তিনি মোল্লার কাছে গিয়েছিলেন তারই কোনো একটা থেকে) যেই তাঁকে আবিষ্কার করে থাকুক-সপ্তাহের শেষে বাড়ি ফেরা কোন তিতিবিরক্ত বিধ্বস্ত কেরানিই হোক কিংবা পান চিবুতে চিবুতে দল বেঁধে যে চাষীরা গাঁয়ের যাত্রা পার্টি দেখতে যাচ্ছিল তারাই হোক-নিশ্চয়ই ধরে নিয়েছিল যে তিনি মরেই গেছেন। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে তারা কোনো হাকিম-বৈদ্যর পরামর্শ নেয়ারও চেষ্টা করেনি-করলে কি আর এখন তিনি এখানে এমনভাবে শুয়ে থাকতেন?’
আলবেয়ার কাম্যুর ‘আউটসাইডার’-এর শুরুয়াত হয়তো এভাবেই বা এভাবে নয়ও একই সঙ্গে কিন্তু মায়ের মৃত্যুর সংশয়বাদী প্রজ্ঞান, সময়হীনতা, অস্তিত্ববাদী-এগজিসটেন্সিলিয়াইজম-সবই আমাদের এক উচ্চাবচ মালভূমির ওপর দাঁড় করিয়ে দেয়, যা খাড়াই পর্বতশিখরে থেকেও বিপজ্জনক ও স্থিতিহীন।
জলহীন সেই মালভূমি বৃক্ষহীনও, যেখানে আছে শুধু শোঁ-শোঁ-শোঁ-বরফিলা বাতাসের শব্দ আর বিপুল অনিশ্চয়তা। যেমন কিনা পৃথিবীর সর্বোচ্চ মালভূমি পামির। সেখানে অবশ্য বরফ বিদ্যমান।
কিয়ের্কে গার্ড, জাঁ পল সার্ত্র, সিমোঁ দ্য বভেয়ার, আলবেয়ার কাম্যু অস্তিবাদের এই সব মহাতালবাদ্যকারীরা আমাদের দার্শনিকভাবে যে যে যে অস্তিত্বহীনতার সামনে দাঁড় করান, তা আলবেয়ার কাম্যুর ‘আউটসাইডার’-এর শুরুর বাক্যটিতেই স্পষ্ট, প্রকট হয়ে ওঠে নায়কের মায়ের মৃত্যুবিষয়ক বাক্যে।
কাজী আনিস আহমেদের এই আখ্যানও শুরু হয় সংশয়াতুর অস্তিত্ব-অনস্তিত্বের প্রশ্ন নিয়ে, যার মধ্যে থাকে প্রাচ্যের দর্শনসংকেত- ‘হইলেও হইতে পারে, আবার না-ও হইতে পারে’, এই দার্শনিক বোধসূত্র লুকনো থাকে, সযতনে।
একটু হেলাফেলা, সারা বেলার ছলেই আখ্যানকার বলতে থাকেন জামশেদপুর নামে এক কল্পশহরের কথা। যার সারা শরীরে মুহূর্তের জন্য ‘মালগুডি ডেজ’-এর আঁইশ-আঁশ জড়ানো থাকলেও অচিরেই মুক্ত হওয়া যায় সেই শল্কল বন্ধন থেকে।
এইখানে জামশেদপুরবিষয়ক দুটি বর্ণনা দেয়ার ইচ্ছে সামলানো গেল না কোনোভাবেই।
তাঁর শোয়ার ঘরের জানালার কাছে দাঁড়িয়েই তিনি দাড়ি কামিয়ে নিয়েছিলেন। জানালা থেকে বড় সড়ক দেখা যায়, জামশেদপুরে সেটাই একমাত্র বাঁধানো রাস্তা। বাকি সবই হয় খোয়া বিছানো আর নয়তো কাঁচা রাস্তা। দিনটা ছিল মঙ্গলবার আর মঙ্গলবারগুলোতেই শুধু দোকানিদের ওই বড় সড়কে পসরা বিছিয়ে বসতে দেয়া হতো-অন্যদিন তারা বসত শহরের ঠিক বাইরেই হাটেবাজারে। শিকদার সাহেবের বাড়ির ঠিক সামনেই বড় সড়কটাকে দখল করে নিয়েছিল মেছোমাইমালেরা। দরাদরির কাংস্যও কণ্ঠগুলো আর মাছ পচার বিদঘুটে গন্ধ শিকদার সাহেবের জানালা দিয়ে এসে হানা দিচ্ছিল।
‘মরশুমের পহেলা ইলিশ’, আবদুল্লাহ মাছওলা চেঁচিয়ে হাঁকছিল।
‘আপনার জামাইয়ের জন্য নিয়ে যান।’
‘ইলিশের দাম কত?’
‘পাঁচশ।’
‘অ্যাঁ! পাঁচশ! পাঁচশ দিয়ে তো আমি গোটা নদীটাই কিনে নিতে পারি, আর এ তো শুধু সামান্য একটা ইলিশ।’
‘হ্যাঁ, তা পারেন, তবে নদীটা বেঁধে রেখে দেখুন কী দাঁড়ায়, আর আমার ইলিশটাকে বেঁধে দেখুন।’ চ্যাটাং করে জবাব দিল আবদুল্লাহ।’ [পৃষ্ঠা ১২]
আবদুল্লাহর জবাব যেন পারিপারিক সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে তৃতীয় দুনিয়ার কোনো ক্রান্তিকারী কণ্ঠস্বর।
জানি না, কথাকার কাজী আনিস আহমেদ তৃতীয় বিশ্বের সামন্ততান্ত্রিক গর্জনের পাল্টা প্রতিগর্জনে-গর্জনাবেশ নিয়েই এই সব কথাযাত্রা নির্মাণ করেন কি না! তবু মনে পড়ার আলোয় এই আখ্যানকারকে বারবার দেখতে থাকি। সুভদ্র, অতিসজ্জন এই কথাকারের সঙ্গে দেখা হয়েছিল ২০১৭-র ঢাকা লিট ফেস্টে। তার আগেও তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে, কলকাতায়, ঢাকাতেও।
থাক সেসব কথাচারণ, আমরা বরং ‘চল্লিশ কদম’-এর কথাচারণে পুনরায় প্রবেশ করি।
‘সত্যিই যদি তাঁর ইন্তেকাল হয়ে গিয়ে থাকে, তবে সেটা মিলিয়ে দেখে নেয়ার একটাই উপায় আছে-পায়ের আওয়াজগুলো গোনা। চল্লিশ কদম। অন্তত মোল্লা তাঁকে এরকমই বলে দিয়েছিল, যে কিনা কোরআন শরিফের সাত-সাতটা প্রচলিত রূপই পড়ে ফেলেছে। সব হাদিসও তার পড়া, এমনকি তেমন নামডাক নেই এমন কেতাবও তার পড়া। এত সব পঠন-পাঠনের পরস্পরবিরোধী তথ্য ছেঁকে নেয়ার পর ইয়াকুব মোল্লা শেষটায় নিশ্চিতভাবে এই তথ্যটা জেনে নিয়েছে: সব মুসলমানকেই কবরে জেরা করতে আসেন দুজন ফেরেশতা, মুনকার আর নাকির। একজন পরপর লিখে নেয় মৃত ব্যক্তি জীবদ্দশায় কী কী সৎ কাজ করেছিল। অন্যজন ফিরিস্তি নেয় সব কাজের।’ [পৃষ্ঠা ৯]
ইসলাম কবুল না করা, ইসলামি মজহরের বাইরের মানুষ হিসেবে অনেকেই হয়তো জানেন না ৭৮৬ এই সংখ্যা বিন্যাসের তাৎপর্য কী। ‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম’ উচ্চারিত হয় কখন। চল্লিশ-এই গাণিতিক পর্যায় সম্বন্ধেও যথেষ্ট ওয়াকিবহাল নন অনেকে।
ইন্তেকাল-মৃত্যুর পর সমাধিভূমির ঘোর অন্ধকারে মাইয়েত বা মাইয়েতাকে গোসল ইত্যাদির পর শুইয়ে দিয়ে, তার ওপর মৃত্তিকা বর্ষণ করার কাজটুকু শেষ হলে, তখনই আসে চল্লিশ কদমের হিসাব।
যিনি সমাধিতে চলে গেলেন, তার রুহ-আত্মার মাগফিরাত কামনা করা হয়। আর ‘মাটি’ হওয়ার চল্লিশ দিনের মাথায় তার ‘কুলপড়া’ বা ‘কুলখানি’।
থাক সেসব প্রসঙ্গ।
এই আখ্যানে মাইয়েত শিকদার সাহেব কবরের গভীরতম প্রদেশে শুয়ে শুয়ে শোক পালনকারীদের ফিরে যাওয়ার খড়ম-ধ্বনি-কাঠের পাদুকার শব্দ শুনতেই থাকেন।
কবরের ‘আজাব’ ইত্যাদি ভাবনাকে দূরে সরিয়ে তিনি গুনতে থাকেন খড়ম-শব্দ-নয়, দশ, এগারো...।
শিকদার সাহেব হাতির দাঁতের বাঁটসমেত ক্ষুর দিয়ে তার ফেনায়িত সাবান মাখানো গালের হজামত করতে থাকেন। কিন্তু একটি বাক্য বিন্যাসে কালো রঙের হাতির দাঁতের তৈরি হাতলের কথা আছে।
এই তথ্যটি খট করে কানে লাগে। হস্তীদন্ত-আইভরি কালো রঙের হয়, এই বিষয়টি আমার অন্তত জানা নেই। আইভরি একটু অফ হোয়াইট। আর সামান্য বিষাদ ছেটানো সাদা বর্ণটি যত পুরোনো ও অ্যানটিকত্ব প্রাপ্তির দিকে এগোয়, তার অফ হোয়াইট মহিমা আরও বেড়ে যেতে থাকে ক্রমে ক্রমে।
শিকদার সাহেব বিষয়ে আমরা যা যা তথ্য পাই, তা এ রকম-
১. শিকদার সাহেব দাঁতের ডাক্তার হতে চেয়েছিলেন, শেষ করতে পারেননি।
২. তার আব্বাজানের ইন্তেকালের পর তিনি জামশেদপুর ফিরে আসেন ও পৈতৃক ওষুধের কারবার-দোকান দেখাশোনার কাজে লেগে যান পুরোদমে।
৩. শিকদার সাহেবের বেগম নূরজাহান। তিনি ও তার বেগমের বসবাস ইংরেজি এল গড়নের একটি একতলা বাড়িতে।
৪. তিনি প্রথম যৌবনে দিব্যি ছিমছাম আর লাজুক। কিন্তু তত দিনে টাক পড়তে শুরু করেছে। ঊনষাট বছর বয়সেই তার মাথায় মস্ত এক টাক, চুলের চিহ্নমাত্র নেই। নাকের ডগায় আছে একটি সাদা গোঁফ। তিনি ধবধবে সাদা পোশাক পরেন।
৫. ডসনের বাবা ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত এক প্রশাসনিক আমলা, দেশ আজাদি পেয়ে যাওয়ার পরও তিনি এ দেশ ছেড়ে চলে যাননি, এ দেশের লোকই হয়ে উঠেছেন। তার গায়ের রংটাও রোদে পুড়ে এমন তামাটে হয়ে গিয়েছে যে যদি তার সোনালি চুল না থাকত, তো সত্যিই ‘দিশি আদমি’ বলে চালিয়ে দিতে পারত।
এই সব তো এই আখ্যানের বহিরঙ্গ-খোসা। ভেতরে-গভীরতম প্রদেশে-আখ্যানকলার নিগূঢ় ছায়ায় থেকে যায় নানা সংকেত ও চিহ্ন। এই কথাযাত্রার অন্যতম চরিত্র মোল্লা সাহেব ও বিদেশ চিত্রকর ডসন। যার দেশ ইংল্যান্ড। মোল্লা সাহেব ও ডসন-স্থবির সামন্ততন্ত্র আর উপনিবেশের দীর্ঘ ছায়া হয়েই যেন চলে আসে আমাদের সামনে।
ছাইরঙা ল্যান্ডরোভারে চেপে যাওয়া-আসা করা প্রত্নতাত্ত্বিকেরা খোঁড়াখুঁড়ি করে খুঁজে বের করেছে কিছু আশ্চর্য ইতিহাসচিহ্ন। জামশেদপুরের মাটির গভীর থেকে ক্রমপ্রকাশিত হয়েছে একটি অতিপ্রাচীন হামাম অথবা হাম্মাম। ‘আর পাশের বিজয়নগর জেলার এক সুপ্রাচীন পয়ঃপ্রণালি নিকাশি ব্যবস্থার ধ্বংসাবশেষ। দুই আবিষ্কারই তারা দাবি করেছে আলমগীর বাদশার সময়কার।’
ডসন তার ঔপনিবেশিক ধ্যানধারণা নিয়ে তার সংগ্রহের টিশিয়ান আর কনস্টেবল, সেই সঙ্গে গোইয়া আর পল গগ্যাঁর ‘কাজ’ দেখাতে থাকে শিকদার সাহেবকে সেখানে-সেই সব চিত্রকর্মে যে নারীরা আছেন, তারা প্রায়শই খোলামেলা পোশাকে।
‘চল্লিশ কদম’-এ আছে মসজিদ-মন্দির বিতর্ক নিয়ে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা।
ডসন একদিকে চিত্রকর আবার প্রত্নতাত্ত্বিকও বটে। ফলে মসজিদের এই জবরদস্ত সাদা মিনার আর গম্বুজ দেখে লোকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকত, বিশেষত তার গায়ে খোদাই করা উজ্জ্বল নীল পদ্মরাগ মণিরত্নের চাঁদ-তারা দেখে লোকে থ হয়ে যেত। আর প্রত্নতাত্ত্বিকেরা সৌধদর্শন শেষ হয়ে যাওয়ার পর তারা তাদের শিবিরে ফিরে গিয়ে নিজেদের মধ্যে ফিসফিসে গলায় বলাবলি করত এ কথাই- ‘এই মসজিদ এককালে নিশ্চয়ই কোনো হিন্দু মন্দির ছিল। মসজিদের পশ্চিম দিকের পাঁচটি পুরনো থাম একেবারেই জীর্ণ দশায় গিয়ে পৌঁছেছে, তাদের সংস্কার বা মেরামত হয়নি, যেমন হয়েছে ওই মসজিদের বাকি অংশের। আড়চোখে সন্তর্পণে তাকিয়ে, প্রত্নতাত্ত্বিকেরা দেখতে পেয়েছে থামের লাল বেলেপাথরের গায়ে নর্তকীদের মূর্তির ভগ্নাংশ। এই সাবুদ যদিও পেশার যন্ত্রপাতি সহযোগে জোগাড় করা হয়নি, তবু যতটুকু দেখা গেছে ততটুকুই তাদের এই হঠাৎ গজানো অনুমানটিকে জোরালই করে দিয়েছে। তাদের মনে কোনো সন্দেহই নেই যে এই মসজিদ একটা মন্দির ছিল।’
কী চমৎকারভাবে অথবা নির্লিপ্ত মানসে বিবরণ থাকে মন্দির-মসজিদ বিতর্কের। ভারতবর্ষে ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ভাঙার যে দুষ্কা-টি সাধিত হয়, তা নিঃসন্দেহে ১৯৪৮-এর ৩০ জানুয়ারি প্রার্থনাসভায় গান্ধীজিকে গুলি করে হত্যা করার যে ভয়ানক কর্ম, তার প্রতিস্পর্ধী অথবা তার থেকেও ভয়ানক হয়ে ওঠে। দাঙ্গা লেগে যায় এই উপমহাদেশে। মহাত্মা গান্ধীকে যে অপশক্তি প্রার্থনাসভায় গুলি করে হত্যা করে, তাদেরই আরেক অংশ ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ ভাঙে। গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষের শাসনক্ষমতাতেও আজ তারাই। এই বিপদ বিন্যাস আমরা কি বুঝতে পারছি? মহাত্মা গান্ধী প্রার্থনাসভায় গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হওয়ার পর এই উপমহাদেশের ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের একাংশ আতঙ্কে ছিলেন, মহাত্মার হত্যাকারী কোনো মুসলমান নন তো! তাহলে তো সেই যুক্তি দেখিয়ে ইসলাম ধর্মের মানুষদের খুলে আম কতল-হত্যা করা সম্ভব হবে।
মসজিদ-মন্দির বিতর্কের মধ্যেই দাঙ্গা লাগে জামশেদপুরে। এই সাম্প্রদায়িক হানাহানির মধ্যেই যা হলো, তা এ রকম।
‘এই আবিষ্কারটা তারা নিজেদের মধ্যে চাপাচুপি দিয়ে রাখবে বলে তারা ঠিক করল কী হবে, কেমন করে যেন কথাটা চাউর হয়ে গেল। স্থানীয় জনসম্প্রদায়ের মধ্যে সে একটা তুমুল হইচই ফেলে দিল। এর ফলে যে দাঙ্গাহাঙ্গামা শুরু হলো তাতে জামশেদপুরের দুই নিচু জাতের হিন্দু খুন হলো। তাদের মুণ্ডহীন শরীরগুলো, বাঁশের গায়ে পা উপরে ধড় নিচে চাপিয়ে বড় সড়কে মিছিল করে ঘুরিয়ে দেখানো হলো। পাশের বিজয়নগর থেকে যখন বদলা নিতে হিন্দুরা এলো তখন খুন হলো মুসলমান মুচি মতি। দেশের অন্যান্য জায়গাতেও এমনিতর নানা ঘটনা ঘটতে লাগল। কোনো এক হিন্দু গাঁয়ে, নাকি জনাকয়েক মুসলমান তরুণী ধর্ষিত হয়েছে। অন্য একটা গাঁয়ে পরদিনই এক হিন্দু সাধুকে জনাকয়েক মুসলমান ছোকরা জোর করে গোরুর গোস্ত খাইয়ে দিয়ে, এসব কথা যতই ফলাও করে দূরদূরান্তে ছড়িয়ে দেয়া হলো, ততই তা ধিক্কার তোলা জনতার রাগকে পুষে রাখতে সাহায্য করল। প্রত্নতাত্ত্বিকরা তাদের পরিকল্পনা শিকেয় তুলে তাদের ল্যান্ডরোভারে করে ঊর্ধ্বশ্বাসে চম্পট দিল। ডসন কিন্তু তাদের সঙ্গে পালাতে পারেনি, কারণ তার তখন বিষম পেটের অসুখ চলছিল।’
এই উপমহাদেশে ভয়ংকর সাম্প্রদায়িক মনোভাব, হানাহানি, ঘৃণা, দ্বেষ কত সহজে সামনে নিয়ে আসেন আখ্যানকার।
আখ্যানকারের জবানিতেই আমরা জানতে পারি-
অসুস্থ ডসনের দেখভাল করার জন্য নূরজাহান একাই উপস্থিত থাকে।
অনুচ্চার্য ইংরেজি শব্দের ভাঁড়ার নূরজাহানের অ্যাতটাই বেড়েছে, যা তার স্বামীকেও ছাড়িয়ে গেছে।
শিকদার সাহেব তার বিবিকে শাদির হপ্তাখানেক বাদে চুম্বন করেছিলেন আর তার কিছু পরেই তারা মিলিত হয়েছিলেন শারীরিকভাবে। আর বিছানাতেই শিকদার সাহেবের বিবি নূরজাহান আদপেই মুখচোরা, লাজুক লবঙ্গলতা নয়... কোনো কোনো নৈশ-অঙ্গচালনার ভাবভঙ্গি শিকদার সাহেবকে একেবারে তাজ্জবই করে দিয়েছিল। তার মনে পড়ে গেল জাহির সাহেবের বইয়ের তাকে তিনি কামসূত্রের একটা ইংরেজি তরজমা দেখেছিলেন।
এই আখ্যান আসলে ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশ জড়িয়ে যে উপমহাদেশ, তারই নানান গলি-ঘুঁজি-অন্ধকার ও বিষাদের কাহিনি।
ফলে এই আখ্যান অনিবার্যভাবেই শেষ হয়ে যায় এভাবে, আবার হয়ও না যেন-
‘ফেরেশতারা আসবে কি না সে সম্বন্ধে তাঁর গভীর সন্দেহ আছে। শুধু যেটা তিনি নিশ্চয় করে জানতে পারবেন সেটা হলো কাঠের ওই পাদুকা জোড়া ক-কদম যায়। কাঠের জুতোর তলির খটখট তিনি শুনতে পাচ্ছেন, ধীরে ধীরে দূরে চলে যাচ্ছে, তবে তা তাঁকে গুনে গুনে হিসাব করা থেকে কিন্তু আটকাতে পারেনি; ছত্রিশ, সাঁইত্রিশ ...’ [পৃষ্ঠা ৬২]
‘পরদিন ভোরবেলা সোনার ডালিম গাছে হাজার ফুল ফুটিয়া উঠিয়াছে;-আর দুপুর বেলা রাজপুরীর তালগাছটা, কিছুর মধ্যে কিছু না, শিকড় ছিঁড়িয়া দুম্ করিয়া পড়িয়া, ফাটিয়া চৌচির হইয়া গেল।’ [ঠাকুরমার ঝুলি, ডালিমকুমার, পৃষ্ঠা ১৪৭]
আমার কথা ফুরোল।
আর নটে গাছটি মুড়োল?
নাহ্, মুড়োল না বোধ হয়।
বাংলাদেশ সময়: ১০০০ ঘণ্টা, সেপ্টেম্বর ২৫, ২০২০
টিএ
